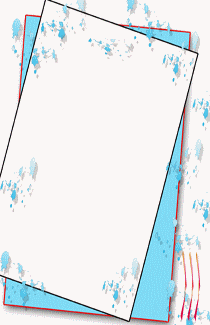ছবি সংগৃহীত
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : সংস্কৃতিতে রাজনীতিকদের উৎসাহহীনতা এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক রুচির দুর্বলতার কারণ হয়তো জ্ঞানের অভাব। সংস্কৃতি কিন্তু জ্ঞানেরও সক্রিয়তার দ্বারা পুষ্ট হয়। জ্ঞানের মূল্য এখন পৃথিবী-জুড়েই কমতির দিকে। জ্ঞানের চাইতে প্রযুক্তির মূল্য অধিক। সাহিত্যেও উৎসাহ কমে আসছে দেখা যায়। নোবেল পুরস্কার তো সেরা সম্মান, কিন্তু সম্প্রতি এক বছর এমন হয়েছে যে, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে একজন সংগীত রচয়িতা ও চর্চাকারীকে, পুরস্কার গ্রহণে যাঁর নিজেরই সংকোচ ছিল। আরেক বছর তো পুরস্কার দেওয়া বন্ধই ছিল, ব্যবস্থাপকদের ভিতর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে। তবে বিশ্বে যাই ঘটুক, আমাদের অবস্থা যে ভালো নয় তা তো মানতেই হবে।
তাই তো দেখা যায় আমাদের রাষ্ট্র জনশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্য যে, ৩২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই আর এটাও জানা গেছে যে, গত ২২ বছর শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের হার একই জায়গাতে অনড় রয়ে গেছে, দক্ষিণ এশিয়াতে যেটি সর্বনিম্ন। এসএসসি পরীক্ষায় নিবন্ধিতদের ভিতর থেকে ৪ লাখের বেশি পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত থেকেছে। কারণ নাকি অভিভাবকদের আর্থিক অসংগতি, জীবিকার প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের কর্মে যোগদান ও কর্মের সন্ধানে বিদেশ গমন এবং অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ। অথচ রাষ্ট্রনায়করা বলেন, অন্যরাও যে বলেন না তা নয়, যে শিক্ষাই আমাদের ভরসা, কারণ আমাদের বিশাল জনসংখ্যাকে যদি কাঁধের বোঝা হিসেবে না রেখে সৃষ্টিশীল সম্পদে পরিণত করতে হয় তাহলে শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। দুই বছরের ব্যবধানে খোদ ঢাকা শহরেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৪ শতাংশ কমেছে। এর বিপরীতে কওমি মাদরাসায় শিক্ষার্থী হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীও বেড়েছে।
অর্থাৎ সমাজের দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়াটা অব্যাহত রয়েছে-একদিকে ধনী, অন্যদিকে দরিদ্র। মধ্যবিত্তের একাংশ (অতি ক্ষুদ্র, অবশ্যই) ওপরের দিকে উঠছে, বড় অংশ নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে, যার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি কিন্ডারগার্টেনের সমৃদ্ধিতে, কওমি মাদরাসার বৃদ্ধিতে এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্ধিষ্ণু দুর্দশায়। ছবিটা নতুন নয়, কিন্তু বিভাজনের মাত্রার এই অগ্রগতি এখন আগের তুলনায় অনেক অধিক। ওদিকে তিন ধারার শিক্ষা তো রয়েছেই। তিন ধারার এক ধারা মাদরাসা শিক্ষা, তার ভিতরেও একাধিক ধারা রয়েছে। এমনকি মূল যে ধারা-বাংলা মাধ্যম, সেখানেও ইংলিশ ভার্সন নামে একটি নতুন অনুষঙ্গের আবির্ভাব ঘটেছে। কথা ছিল সর্বস্তরে শিক্ষার ধারা হবে এক এবং অভিন্ন এবং তার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। প্রাথমিক পর্যায়ে, অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শেখার দরকার নেই; প্রাথমিক পার হয়ে শিক্ষার্থীরা বিদেশি একটি ভাষা শিখবে (প্রধানত ইংরেজি) এমনটাই ছিল ধারণা। সেসব স্বপ্ন এখন ভগ্নস্তূপ বৈ নয়।
শিক্ষা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করছে না, বরং শ্রেণি বিভাজনকেই আরও গভীর এবং ব্যাপক সংস্কৃতিতে রাজনীতিকদেরকরে একটি অভিন্ন সংস্কৃতি সৃষ্টির সম্ভাবনাকে প্রতিহত করে চলেছে। কিন্ডারগার্টেন ব্যবসা হিসেবেও খারাপ নয়। অন্যদিকে কওমি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা বিশেষ ব্যয়বহুল নয়, মসজিদকে ব্যবহার করলেই চলে। এর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি তৈরিও কঠিন নয়। কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা হিসেবে যা দেওয়া হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তা যে দাবি করবেন, এমন সাহস রাখেন না। অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা বলেছেন, সম্পদের অপ্রতুলতার জন্য শিক্ষকদের তাঁরা প্রাপ্য মর্যাদা দিতে পারছেন না। কথাটা দুই দিক থেকেই সঠিক। শিক্ষকরা মর্যাদা পাচ্ছেন না এবং তাঁদের জন্য বরাদ্দও সংকীর্ণ। কিন্তু এই বাস্তবতা কোনো রাজনৈতিক ভূমিকম্পের দরুন সৃষ্টি হয়নি; এটি ঘটেছে উন্নয়নের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ও ধারাবাহিকতায়। রাষ্ট্র যাঁরা চালান তাঁরা সাধারণ মানুষের শিক্ষা নিয়ে মোটেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নন, তাঁদের চিন্তা নিজেদের সন্তানকে কেমন করে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াবেন এবং কত দ্রুত বিদেশে পাঠানো যায় তা নিয়ে।
সংস্কারের প্রয়োজনে অন্তর্বর্তী সরকার ১১টি কমিশন গঠন করেছে, কিন্তু তাঁরা শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে যে কোনো কমিশন গঠন করেনি এজন্য অবশ্যই প্রশংসা দাবি করতে পারেন। আমাদের মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা এমনিতেই নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে, তার মধ্যে আবার সংস্কারের ধাক্কাধাক্কি সে-বেচারাকে নতুন জ¦ালাতনের মধ্যে ফেলুক, এটা মোটেই কাক্সিক্ষত নয়। অতীতে দেখা গেছে যে, যখনি কোনো ‘বৈপ্লবিক’ সরকারের আগমন ঘটে, তখনি, সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়েন এবং মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা একটা ধাক্কা খায়। পরবর্তী ‘বিপ্লবী’ সরকার আবার নতুন সংস্কারে হাত লাগিয়ে ব্যবস্থাটাকে আরেকটা ধাক্কা দেন। মূল যে সংস্কার প্রয়োজন সেটা হলো একটি অভিন্ন ব্যবস্থা চালু করা। রাষ্ট্র পরিচালকরা সে ব্যাপারটাকে বিবেচনার মধ্যেই আনেন না। বৈষম্যনির্ভর পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা আগের মতোই সহাস্যে টিকে থাকে।
পতিত আওয়ামী সরকার সংস্কারের নাম করে কয়েকটি অতিরিক্ত পাবলিক পরীক্ষার সংযোজন ঘটিয়ে মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি সাধনে তৎপর হয়েছিলেন, তাতে দুর্বল ব্যবস্থাটা আরও একটা ঝুঁকির মুখে পড়েছিল। বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ ওঠায় তারা অতিরিক্ত পরীক্ষা রদ করেন। কিন্তু ২০১৭ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যে তাদের নিজেদের প্রণীত বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে আচমকা ১১টি কবিতা এবং পাঁচটি গল্প ও প্রবন্ধ বাদ দিয়ে দিল, সেই বৈপ্লবিক কাজটি কেন করা হলো তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। বিগত সরকারের পতনের পর তাদের অনেক নৃশংসতা, অপকর্ম ও দুর্নীতির তদন্ত করা হচ্ছে এবং হতে থাকবে, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের ওপর নির্মম ও ক্ষতিকর হামলাটি কেন ঘটেছিল, সে বিষয়ে কোনো তদন্ত হয়নি। তদন্ত হওয়াটা কিন্তু আবশ্যক। জানা দরকার, শিক্ষার ওপর অমন হস্তক্ষেপটি কারা এবং কীভাবে ঘটিয়েছিল। কাজটা বর্তমান সরকার শিক্ষাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে সেটা জানার ব্যাপারেও সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।
ফ্যাসিবাদ আসলে, নিজেদের যারা উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক ইত্যাদি বলতে ভালোবাসেন তাদের মধ্যে যে আছে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা তা বিশেষভাবে জেনেছি। আর ধর্মকে যারা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে তাদের ভিতর যে কী পরিমাণে আছে সেটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে আমরা একাত্তরেই দেখেছি। ভারতে যে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এখন রাজত্ব করছেন, তারা তো দেখা যাচ্ছে হত্যাকণ্ডে খুবই সিদ্ধহস্ত। মহাত্মা গান্ধীকে পর্যন্ত তারা ক্ষমা করেননি; সামনাসামনি গুলি করে হত্যা করেছে।
বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী আবার প্রকাশ্যে রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। গুপ্ত অবস্থায় থেকে হিযবুত তাহ্রীরও তৎপর হয়ে উঠেছে। লক্ষ করা যাচ্ছে হেফাজতে ইসলামের কাজকর্মও। তাদের সমাবেশে লোকের অভাব ঘটে না।
তেমন একটা ওয়াজই সেদিন ভিন্ন আঙ্গিকে চলে এসেছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, হেফাজতিদের সমাবেশে। সংস্কারের মহৎ উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে গঠিত যে ১১টি কমিশন কাজ করছে, তাদের অন্য কোনোটির বিষয়েই হেফাজতিরা একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কেবল একটির ওপরে; সেটি হলো নারীর অধিকারবিষয়ক সংস্কার কমিশন। সেই কমিশন অবিলম্বে ভেঙে দিতে হবে বলে তাঁরা হুংকার দিয়েছেন। কমিশন অন্য কেউ গঠন করেনি, করেছে সরকার নিজে। সেই কমিশন ভেঙে দিতে হবে এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের দিক থেকে প্রতিবাদ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ আমরা শুনিনি।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । সূএ: বাংলাদেশ প্রতিদিন