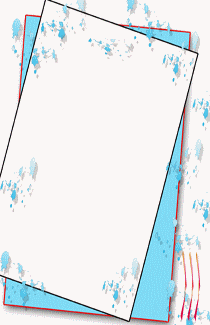মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার পিএসসি (অব.) : শোকের মাস চলছে। ১৫ আগস্ট ছিল জাতীয় শোক দিবস। যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি পালন করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে সংঘটিত জাতীয় ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও রাজনীতির যে হিমালয়সম ক্ষতি হয়েছে, তা কোনো দিন পূরণ হবে কি না, সে এক বিরাট প্রশ্ন। বাংলাদেশে বড় এক রাজনৈতিক পক্ষ শোক দিবস পালন করে না। তারা এখনো রাজপথে প্রকাশ্যে স্লোগান দেয়, পঁচাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার। অর্থাৎ পঁচাত্তরের হত্যাকান্ডকে তারা এখনো সমর্থন দিচ্ছে। রাস্তায় রাজনীতিতে অহরহ স্লোগান হচ্ছে, জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো। এরকম ফৌজদারি অপরাধ সমতুল্য স্লোগান দেওয়ার পরও রাষ্ট্রের আইনি কর্তৃপক্ষ যখন পদক্ষেপ কোনো নেয় না, তখন বুঝতে হবে, হত্যা, সন্ত্রাস ও জ্বালাও পোড়াওয়ের রাজনীতি বাংলাদেশে এখনো জায়েজ বা বিধিসম্মত। ফলে জাতির পিতাকে অস্বীকার, অসম্মান, ছোট করে এবং মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সব রাজনৈতিক ইতিহাস ও মূল্যবোধকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও অমান্য করে বাংলাদেশে রাজনীতি করা যায় এবং ক্ষমতায়ও যাওয়া যায়। সুতরাং এসব নিয়ে রাজনীতিকরা মাথা ঘামান না। এর থেকে রাষ্ট্রকে বের করে আনার জন্য যা করণীয় তা কেউ করছে না, অথবা আপেক্ষিকতার সূত্রে বলা যায়, কেউ কিছু করতে পারছেন না। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য হুমকিসম কর্মকান্ড করে পার পাওয়া যায়। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ আর বিপক্ষের রাজনৈতিক সংঘাতের ফাঁক দিয়ে গোষ্ঠীতন্ত্র রাষ্ট্রের চেয়ে বড় ক্ষমতাবান হয়ে যাচ্ছে। এর অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। বছরের পর বছর ধরে সড়ক-মহাসড়কে প্যান্ডেসিকের চেয়েও বেশি মানুষের মৃত্যুর পথ-রোধ করা যাচ্ছে না, একক কোনো রাজনৈতিক পক্ষ, ক্ষমতার ভিতরে বা বাইরে থেকে করতে গেলে, যে পক্ষ কিছু করতে চাইবে তার বিপরীত পক্ষ রাজনৈতিক সুবিধা ও ভোটের সুবিধার জন্য ওই মার্ডারারদের পক্ষ নেবে, এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। রাষ্ট্র, সমাজ ও সংগঠনের সর্বত্র রাজনীতিগতভাবে এমন চরম বিভাজনকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসেও ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করতে হয়। সত্তর-একাত্তরে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে যেভাবে, যে মাত্রায় ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, তা কি আর কখনো হবে। হবে কী করে, রাজনীতি এখন মানি আর মাসলের কবজায়। এর সঙ্গে আরেকটি শক্তি যোগ হয়েছে, যার নাম .jpg) ধর্মীয় উন্মাদনা। একটা নির্দিষ্ট পোশাক পরে লাঠিসোঁটা নিয়ে বেশি নয়, ২-৩ হাজার লোক রাস্তায় নেমে নির্দিষ্ট কিছু স্লোগান দিলে তাদের আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। কিছু বললে ধর্মের অবমাননা হবে। আর কিছু লোক বড় বড় পোশাক পরে নামের আগে-পরে আমাদের মতো মূর্খদের বোঝার উপায় নেই এমন আরবি ভাষায় ডজনখানেক পদবি ও খেতাব নিয়ে ধর্মের যে ব্যাখ্যা দেবে সবাইকে সেটা মানতে হবে। খেতাব ও পদবি লিখতে তারা কখনো বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন না। এনাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা সমালোচনা করা যাবে না। সুতরাং রাজনীতি যেদিকে ধাবিত হচ্ছে তা বাংলাদেশের জন্য বিপৎসংকেত, যে কথা বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বলে গেছেন। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, অসাম্প্রদায়িক আদর্শকে রক্ষা করতে না পারলে বাংলাদেশকে রক্ষা করা যাবে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বয়স ৫১ বছর। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় রাষ্ট্রগুলো থিতু হতে যত সময় নিয়েছে, সেই বিচারে ৫১ বছর খুব বেশি সময় নয়। মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলেই সব অনাচার দূর করা সম্ভব। সত্তর-একাত্তরে দেশের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানি, মাসল ও ধর্মীয় উন্মাদনার রাজনীতিকে বিদায় করে দিয়েছিল। এত সংগ্রাম, এত ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত সর্বজনগ্রাহ্য রাজনৈতিক মূল্যবোধ কেন এরকম মারণব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হলো তার বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রয়োজন এ কারণে যে, যত সময় লাগুক, যত যা কিছু করা লাগুক হত্যা, সন্ত্রাস ও ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে, যদি আমরা স্বাধীন বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখতে চাই। তাই কেন এরকম হলো সেটাই প্রথমে বোঝা দরকার। একটি রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৭১ সালে। এর আগে আমরা একবার স্বাধীতা পেয়েছিলাম ১৯৪৭ সালে। সুতরাং ১৯৭১ সালে শুধু স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে আমাদের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বাধীনতার পথ ধরে সব ধরনের বঞ্চনা, বৈষম্য আর সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মুক্তি অর্জনই ছিল চূড়ান্ত লক্ষ্য। ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকরা ধর্মীয় উগ্রবাদের শিকলে বন্দি করে সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং বাঙালি পরিচয়টিকেও বিলুপ্ত করতে চেয়েছে ধর্মের দোহাই দিয়ে। তার জন্য ১৯৭১ সালের ৯ মাসের যুদ্ধটিকে মুক্তিযুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। একই কারণে বাহাত্তরের সংবিধানের একেবারে প্রথম তিনটি লাইনে প্রস্তাবনার অংশ হিসেবে লেখা হয়- ‘আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। উগ্র-ধর্মীয় চেতনাপ্রসূত ধর্মীয় রাজনীতি, বাঙালি সংস্কৃতি মুসলমানের সংস্কৃতি নয় এবং একমাত্র সামরিক বাহিনীই পাকিস্তানের রক্ষাকবচ- এই তিন উপাদান ও অভিধাকে অবলম্বন করে ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের শৃঙ্খলবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেছে। যখনই বাঙালি নিজেদের ন্যায্য অধিকার চেয়েছে, তখনই পাকিস্তানি শাসকরা প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে এই মর্মে যে, বাঙালিরা খাঁটি মুসলমান নয়, বাঙালির সবকিছু হলো হিন্দুয়ানায় ভরপুর, এরা সব ভারতের দালাল ও পাকিস্তানের শত্রু। তাই ধর্মীয় রাজনীতি, বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অপবাদ এবং সব ধরনের শোষণ ও অধিকারহীনতার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দীর্ঘ মুক্তি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একাত্তরে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পঁচাত্তরের পরে দুই সামরিক শাসকের হাত ধরে যেসব রাজনৈতিক পক্ষের উত্থান ঘটেছে তারা এবং একাত্তরের পরাজিত জামায়াত মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য পাকিস্তানি সহযোগী দলসমূহের পুরনো নতুন প্রজন্মের সবাই ওই পাকিস্তানিদের মতোই একই রকম গালি দেয় তাদের। যারা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, দর্শন ও মূল্যবোধকে ধারণ এবং তার বিস্তারে কাজ করেন। সে জন্যই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, শুধু শাসক পরিবর্তন করে লাভ হবে না, আদর্শ, দর্শন ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধু সব ঠিক করে যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু যাত্রার শুরুতেই সব যেভাবে শেষ হয়ে গেল সেটা জানা-বোঝার দরকার? পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুযোগে ১৯৭২ সালে রাজনৈতিক দল জাসদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এক সময়ে তারা সশস্ত্র গণবাহিনী গঠন করে। তখন অবৈধ অস্ত্র জোগাড় ছিল সহজলভ্য। এই গণবাহিনীর হাত ধরেই বাংলাদেশে হত্যাকান্ডের রাজনীতি শুরু হয়। জামায়াত, মুসলিম লীগসহ পাকিস্তানের সব সহযোগী রাজনীতি তখন নিষিদ্ধ থাকায় সুযোগ পেয়ে নিজেদের গ্লানি ঢাকা দিতে তারা জাসদের রাজনীতির পতাকাতলে আশ্রয় নেয়। ফলে একটি রাজনৈতিক দল জন্ম নেওয়ার এক বছর না যেতেই বড় এক সংখ্যক মানুষের সমর্থন পেয়ে যায়, যা ছিল আরেক বড় অস্বাভাবিক ঘটনা। একাত্তরে প্রায় শতকরা ২০-২৫ ভাগ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল। তার মানে প্রায় দেড় দুই কোটি মানুষের রেডিমেড সমর্থন পেয়ে যায় জাসদ। এদের মধ্যে থেকে ‘গণবাহিনীতে যোগ দেয় একাংশ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে হত্যাকান্ডের পথ বেছে নেয় গণবাহিনী। শুধু ১৯৭৩ সালেই ৭০টি থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুট হয়। জাতীয় সংসদের বিবরণ অনুযায়ী শুধু ১৯৭৩ সালেই ১ হাজার ৮৯৬টি হত্যাকান্ড ঘটে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত সাতজন সংসদ সদস্যকে হত্যা করা হয়। হত্যাকান্ডের শিকার হন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে এক দিনে একসঙ্গে ২৭টি পাটের গুদামে আগুন দেওয়া হয়। উপরোক্ত সব হত্যাকান্ডের শিকার হন আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা। এরকম এক প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের সিঁড়ি বেয়ে সেনাবাহিনীর কাঁধে ভর করে এক সময় রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন প্রথম সামরিক প্রশাসক ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান। প্রথমে খন্দকার মোশতাক অর্ডিন্যান্স জারি করেন এবং পরে জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বঘোষিত হত্যাকারীদের বিচারের পথ বন্ধ করে দেন। তারপর হত্যাকারীদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি দেন। আর এভাবেই বাংলাদেশে হত্যাকান্ডের রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এখান থেকেই সন্ত্রাসের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা শুরু। এই যে শুরু হলো হত্যাকান্ডের রাজনীতি, যার লেগেসির প্রভাব আমাদের রাজনীতিতে এখনো বিদ্যমান। পঁচাত্তরের রক্তের সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশে যে রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু হলো, তাতে মুক্তিযুদ্ধের দর্শন ও আদর্শ বলতে আর কিছু থাকল না। সবকিছুতে পাকিস্তানিকরণ হয়ে গেল। ফলে হত্যাকান্ডের রাজনীতির পথ আরও প্রশস্ত হলো। সেই পথ ধরে ১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়াউর রহমানও নির্মমভাবে নিহত হলেন। তার প্রতিষ্ঠিত দল ও স্ত্রী-পুত্র পরবর্তীতে ক্ষমতায় থাকার পরেও একজন সিটিং রাষ্ট্রপতি হত্যার বিচার কেউ চাইল না। দ্বিতীয় সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ তার পূর্বসূরির ধারাবাহিকতা শুধু রক্ষা করেছেন তা নয়, আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশকে পাকিস্তানকরণের অদম্য চেষ্টার অংশ হিসেবে উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানসহ সংবিধানে সন্নিবেশিত করেন রাষ্ট্র ধর্ম। দুই সামরিক শাসক কর্তৃক একাত্তরের পরাজিত মুসলিম লীগ, জামায়াতসহ উগ্রবাদী গোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের কারণে বাংলাদেশে হত্যাকান্ডের রাজনীতির আরেকটি ধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তারা রাজনৈতিক লক্ষ্য অজনের জন্য বিভিন্ন নামে সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠন তৈরি করে, জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ, হিযবুত তাহরীর, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ইত্যাদি। এদের টার্গেট হন তারাই, যারা মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি সংস্কৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন এবং তার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। সুতরাং সশস্ত্র জঙ্গিরা যেসব হত্যাকান্ড চালায় তার লক্ষ্যও স্পষ্টতই রাজনৈতিক। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, যারা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিরুদ্ধে রাজনীতি করেন এবং ধর্মতন্ত্রের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, তাদের একজন ব্যক্তির গায়েও জঙ্গিদের সামান্য টোকা পর্যন্ত লাগেনি। সুতরাং জঙ্গি সংগঠন কর্তৃক হত্যাকান্ডের পেছনে প্রকাশ্যভাবে ধর্মীয় রাজনীতি দায়ী। তাই এগুলোও হত্যাকান্ডের রাজনীতির অংশ, যার শুরু ১৯৭৫ সালের পর থেকে। হত্যাকান্ডের রাজনীতির আরেকটি বড় ও নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট। ওই দিন তখনকার বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার জনসভার ওপর প্রকাশ্য দিবালোকে ভয়াবহ গ্রেনেড আক্রমণ হয়। তাতে ঘটনাস্থলেই আওয়ামী লীগের ২৪ নেতা-কর্মী নিহত হন। তখন জামায়াত-বিএনপি সরকার হত্যার দায় ভিন্ন খাতে নেওয়ার জন্য জজ মিয়া নাটক সাজানোর কারণে এবং পরবর্তীতে বিচারিক আদালতের রায়ের পর্যবেক্ষণে বোঝা যায়, সেই আক্রমণ পরিচালিত হয় তখনকার সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায়। দুঃখজনক হলেও সত্য, হত্যাকান্ডের রাজনীতি থেকে আমরা আজও বের হতে পারলাম না, এখনো রাস্তায় স্লোগান হয় ‘পঁচাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার’। তাতে বোঝা যায়, যারা হত্যাকান্ডের রাজনীতির সুবিধাভোগী তারা কখনো এর থেকে বের হতে চাইবে না, পারবেও না। একমাত্র জনগণই এই কলঙ্ক থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে পারে।
ধর্মীয় উন্মাদনা। একটা নির্দিষ্ট পোশাক পরে লাঠিসোঁটা নিয়ে বেশি নয়, ২-৩ হাজার লোক রাস্তায় নেমে নির্দিষ্ট কিছু স্লোগান দিলে তাদের আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। কিছু বললে ধর্মের অবমাননা হবে। আর কিছু লোক বড় বড় পোশাক পরে নামের আগে-পরে আমাদের মতো মূর্খদের বোঝার উপায় নেই এমন আরবি ভাষায় ডজনখানেক পদবি ও খেতাব নিয়ে ধর্মের যে ব্যাখ্যা দেবে সবাইকে সেটা মানতে হবে। খেতাব ও পদবি লিখতে তারা কখনো বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন না। এনাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা বা সমালোচনা করা যাবে না। সুতরাং রাজনীতি যেদিকে ধাবিত হচ্ছে তা বাংলাদেশের জন্য বিপৎসংকেত, যে কথা বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বলে গেছেন। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, অসাম্প্রদায়িক আদর্শকে রক্ষা করতে না পারলে বাংলাদেশকে রক্ষা করা যাবে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বয়স ৫১ বছর। ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় রাষ্ট্রগুলো থিতু হতে যত সময় নিয়েছে, সেই বিচারে ৫১ বছর খুব বেশি সময় নয়। মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলেই সব অনাচার দূর করা সম্ভব। সত্তর-একাত্তরে দেশের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানি, মাসল ও ধর্মীয় উন্মাদনার রাজনীতিকে বিদায় করে দিয়েছিল। এত সংগ্রাম, এত ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত সর্বজনগ্রাহ্য রাজনৈতিক মূল্যবোধ কেন এরকম মারণব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হলো তার বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রয়োজন এ কারণে যে, যত সময় লাগুক, যত যা কিছু করা লাগুক হত্যা, সন্ত্রাস ও ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে, যদি আমরা স্বাধীন বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখতে চাই। তাই কেন এরকম হলো সেটাই প্রথমে বোঝা দরকার। একটি রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৭১ সালে। এর আগে আমরা একবার স্বাধীতা পেয়েছিলাম ১৯৪৭ সালে। সুতরাং ১৯৭১ সালে শুধু স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে আমাদের লক্ষ্য সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বাধীনতার পথ ধরে সব ধরনের বঞ্চনা, বৈষম্য আর সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে মুক্তি অর্জনই ছিল চূড়ান্ত লক্ষ্য। ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকরা ধর্মীয় উগ্রবাদের শিকলে বন্দি করে সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং বাঙালি পরিচয়টিকেও বিলুপ্ত করতে চেয়েছে ধর্মের দোহাই দিয়ে। তার জন্য ১৯৭১ সালের ৯ মাসের যুদ্ধটিকে মুক্তিযুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। একই কারণে বাহাত্তরের সংবিধানের একেবারে প্রথম তিনটি লাইনে প্রস্তাবনার অংশ হিসেবে লেখা হয়- ‘আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। উগ্র-ধর্মীয় চেতনাপ্রসূত ধর্মীয় রাজনীতি, বাঙালি সংস্কৃতি মুসলমানের সংস্কৃতি নয় এবং একমাত্র সামরিক বাহিনীই পাকিস্তানের রক্ষাকবচ- এই তিন উপাদান ও অভিধাকে অবলম্বন করে ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের শৃঙ্খলবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেছে। যখনই বাঙালি নিজেদের ন্যায্য অধিকার চেয়েছে, তখনই পাকিস্তানি শাসকরা প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে এই মর্মে যে, বাঙালিরা খাঁটি মুসলমান নয়, বাঙালির সবকিছু হলো হিন্দুয়ানায় ভরপুর, এরা সব ভারতের দালাল ও পাকিস্তানের শত্রু। তাই ধর্মীয় রাজনীতি, বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অপবাদ এবং সব ধরনের শোষণ ও অধিকারহীনতার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দীর্ঘ মুক্তি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একাত্তরে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পঁচাত্তরের পরে দুই সামরিক শাসকের হাত ধরে যেসব রাজনৈতিক পক্ষের উত্থান ঘটেছে তারা এবং একাত্তরের পরাজিত জামায়াত মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য পাকিস্তানি সহযোগী দলসমূহের পুরনো নতুন প্রজন্মের সবাই ওই পাকিস্তানিদের মতোই একই রকম গালি দেয় তাদের। যারা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, দর্শন ও মূল্যবোধকে ধারণ এবং তার বিস্তারে কাজ করেন। সে জন্যই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, শুধু শাসক পরিবর্তন করে লাভ হবে না, আদর্শ, দর্শন ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধু সব ঠিক করে যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু যাত্রার শুরুতেই সব যেভাবে শেষ হয়ে গেল সেটা জানা-বোঝার দরকার? পার্লামেন্টারি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুযোগে ১৯৭২ সালে রাজনৈতিক দল জাসদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এক সময়ে তারা সশস্ত্র গণবাহিনী গঠন করে। তখন অবৈধ অস্ত্র জোগাড় ছিল সহজলভ্য। এই গণবাহিনীর হাত ধরেই বাংলাদেশে হত্যাকান্ডের রাজনীতি শুরু হয়। জামায়াত, মুসলিম লীগসহ পাকিস্তানের সব সহযোগী রাজনীতি তখন নিষিদ্ধ থাকায় সুযোগ পেয়ে নিজেদের গ্লানি ঢাকা দিতে তারা জাসদের রাজনীতির পতাকাতলে আশ্রয় নেয়। ফলে একটি রাজনৈতিক দল জন্ম নেওয়ার এক বছর না যেতেই বড় এক সংখ্যক মানুষের সমর্থন পেয়ে যায়, যা ছিল আরেক বড় অস্বাভাবিক ঘটনা। একাত্তরে প্রায় শতকরা ২০-২৫ ভাগ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল। তার মানে প্রায় দেড় দুই কোটি মানুষের রেডিমেড সমর্থন পেয়ে যায় জাসদ। এদের মধ্যে থেকে ‘গণবাহিনীতে যোগ দেয় একাংশ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে হত্যাকান্ডের পথ বেছে নেয় গণবাহিনী। শুধু ১৯৭৩ সালেই ৭০টি থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুট হয়। জাতীয় সংসদের বিবরণ অনুযায়ী শুধু ১৯৭৩ সালেই ১ হাজার ৮৯৬টি হত্যাকান্ড ঘটে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত সাতজন সংসদ সদস্যকে হত্যা করা হয়। হত্যাকান্ডের শিকার হন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে এক দিনে একসঙ্গে ২৭টি পাটের গুদামে আগুন দেওয়া হয়। উপরোক্ত সব হত্যাকান্ডের শিকার হন আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা। এরকম এক প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের সিঁড়ি বেয়ে সেনাবাহিনীর কাঁধে ভর করে এক সময় রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন প্রথম সামরিক প্রশাসক ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান। প্রথমে খন্দকার মোশতাক অর্ডিন্যান্স জারি করেন এবং পরে জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বঘোষিত হত্যাকারীদের বিচারের পথ বন্ধ করে দেন। তারপর হত্যাকারীদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি দেন। আর এভাবেই বাংলাদেশে হত্যাকান্ডের রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এখান থেকেই সন্ত্রাসের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা শুরু। এই যে শুরু হলো হত্যাকান্ডের রাজনীতি, যার লেগেসির প্রভাব আমাদের রাজনীতিতে এখনো বিদ্যমান। পঁচাত্তরের রক্তের সিঁড়ি বেয়ে বাংলাদেশে যে রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু হলো, তাতে মুক্তিযুদ্ধের দর্শন ও আদর্শ বলতে আর কিছু থাকল না। সবকিছুতে পাকিস্তানিকরণ হয়ে গেল। ফলে হত্যাকান্ডের রাজনীতির পথ আরও প্রশস্ত হলো। সেই পথ ধরে ১৯৮১ সালের ৩০ মে জিয়াউর রহমানও নির্মমভাবে নিহত হলেন। তার প্রতিষ্ঠিত দল ও স্ত্রী-পুত্র পরবর্তীতে ক্ষমতায় থাকার পরেও একজন সিটিং রাষ্ট্রপতি হত্যার বিচার কেউ চাইল না। দ্বিতীয় সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদ তার পূর্বসূরির ধারাবাহিকতা শুধু রক্ষা করেছেন তা নয়, আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশকে পাকিস্তানকরণের অদম্য চেষ্টার অংশ হিসেবে উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানসহ সংবিধানে সন্নিবেশিত করেন রাষ্ট্র ধর্ম। দুই সামরিক শাসক কর্তৃক একাত্তরের পরাজিত মুসলিম লীগ, জামায়াতসহ উগ্রবাদী গোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের কারণে বাংলাদেশে হত্যাকান্ডের রাজনীতির আরেকটি ধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তারা রাজনৈতিক লক্ষ্য অজনের জন্য বিভিন্ন নামে সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠন তৈরি করে, জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ, হিযবুত তাহরীর, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ইত্যাদি। এদের টার্গেট হন তারাই, যারা মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি সংস্কৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন এবং তার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। সুতরাং সশস্ত্র জঙ্গিরা যেসব হত্যাকান্ড চালায় তার লক্ষ্যও স্পষ্টতই রাজনৈতিক। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, যারা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিরুদ্ধে রাজনীতি করেন এবং ধর্মতন্ত্রের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, তাদের একজন ব্যক্তির গায়েও জঙ্গিদের সামান্য টোকা পর্যন্ত লাগেনি। সুতরাং জঙ্গি সংগঠন কর্তৃক হত্যাকান্ডের পেছনে প্রকাশ্যভাবে ধর্মীয় রাজনীতি দায়ী। তাই এগুলোও হত্যাকান্ডের রাজনীতির অংশ, যার শুরু ১৯৭৫ সালের পর থেকে। হত্যাকান্ডের রাজনীতির আরেকটি বড় ও নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট। ওই দিন তখনকার বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার জনসভার ওপর প্রকাশ্য দিবালোকে ভয়াবহ গ্রেনেড আক্রমণ হয়। তাতে ঘটনাস্থলেই আওয়ামী লীগের ২৪ নেতা-কর্মী নিহত হন। তখন জামায়াত-বিএনপি সরকার হত্যার দায় ভিন্ন খাতে নেওয়ার জন্য জজ মিয়া নাটক সাজানোর কারণে এবং পরবর্তীতে বিচারিক আদালতের রায়ের পর্যবেক্ষণে বোঝা যায়, সেই আক্রমণ পরিচালিত হয় তখনকার সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায়। দুঃখজনক হলেও সত্য, হত্যাকান্ডের রাজনীতি থেকে আমরা আজও বের হতে পারলাম না, এখনো রাস্তায় স্লোগান হয় ‘পঁচাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার’। তাতে বোঝা যায়, যারা হত্যাকান্ডের রাজনীতির সুবিধাভোগী তারা কখনো এর থেকে বের হতে চাইবে না, পারবেও না। একমাত্র জনগণই এই কলঙ্ক থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে পারে।
[email protected] সূএ: বাংলাদেশ প্রতিদন