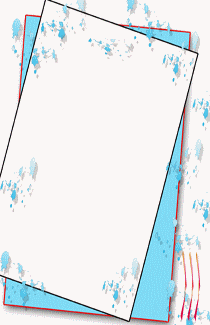ছবি সংগৃহীত
অনলাইন ডেস্ক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জুলাই আন্দোলনে আহত হওয়া সানজিদা আহমেদ তন্বি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে সানজিদা আহমেদ তন্বি তার অর্জন, গবেষণা ও প্রকাশনায় অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনী ইশতেহার তুলে ধরেন।
গবেষণা ও অ্যাকাডেমিক প্রকাশনায় নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের প্রথম গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই তার মূল লক্ষ্য বলে তার নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করেছেন তিনি।
‘আমার অ্যাকাডেমিক অর্জন, গবেষণা ও প্রকাশনায় অভিজ্ঞতা ও ইশতেহার’ শিরোনামে তন্বির লেখা পোস্টটি পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো-
‘আমি সানজিদা আহমেদ তন্বি। আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে ‘গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক’ হিসেবে নির্বাচন করছি। এই পদে নির্বাচন করার কারণ আমার অভিজ্ঞতা ও এই সেক্টর নিয়ে কাজ করার আগ্রহ। আমার অ্যাকাডেমিক অর্জন ও গবেষণায় অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি—
১. স্নাতকে বিভাগে আমার অবস্থান তৃতীয়। চতুর্থ বর্ষে জুলাই আন্দোলনের আগে ও পরে ঢাকার ২০টি স্কুলের ৪০০ এর মতো স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে, ডেটা সংগ্রহ করে একটি রিসার্চ সম্পন্ন করেছি। এরই মধ্যে রিসার্চ পেপারটি ‘Educational studies’ নামক একটি পিআর-রিভিউড জার্নালে পাবলিকেশনের অপেক্ষায়। এটির ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর ১.৬ (Q2) , সাইট স্কোর ৭.২ (Q1)।
২. মাস্টার্সেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমার একটি রিসার্চ চলমান। সেটি এরই মধ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ফেলোশিপের জন্য শর্টলিস্টেড হয়েছে।
অনার্স ও মাস্টার্সের গবেষণার পাশাপাশি আমি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকল্পে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যুক্ত আছি। এর মধ্যে রয়েছে—
৩. ইউনেস্কো ও মাউশির যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত Health Promoting School Project।
৪. ইউনেস্কো ও ইউজিসির যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত Social Emotional Well-being of University Students প্রজেক্ট।
৫. ইউনিসেফ ও ইউজিসির যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত Social Behavioral Change & Community Engagement প্রজেক্ট।
এছাড়াও সেন্টার ফর সাইকোলজিক্যাল হেলথ এর রিসার্চ টিমে যুক্ত আছি।
আমার ইশতেহার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। কিন্তু বাস্তবতা হলো আমরা অক্সফোর্ডের থেকে অনেক পিছিয়ে আছি। এর পেছনে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি একটি বড় কারণ। তবে, দেশের যে সামান্য রিসোর্স আছে, সেটার সঠিক ব্যবহারও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে হয় না। ফলস্বরূপ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনো বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ৫০০-এর বাইরে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো গবেষণার সুযোগ ও বাজেটের ঘাটতি।
বিগত অর্থবছরের চেয়ে চলতি অর্থবছরে গবেষণা বাজেট বেড়েছে যৎসামান্য। চলতি অর্থবছরে ১ হাজার ৩৫ কোটি ৪৫ লাখ টাকার মোট বাজেটে গবেষণার জন্য রাখা হয়েছে কেবল ২১ কোটি ৫৭ লাখ, যা মোট বাজেটের ২ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। আগের অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২০ কোটি ৭ লাখ টাকা। নতুন বাংলাদেশে এটি আশাব্যঞ্জক নয়।
সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ হাজার ৮৪০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। সর্ববৃহৎ এই অবকাঠামোগত প্রকল্পের মতো শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন ও পঠন-পাঠন পদ্ধতির উন্নয়নেও সমান গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশকে গর্বিত করার মতো জায়গায় নিতে হলে গুরুত্ব দিতে হবে গবেষণা ও প্রকাশনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (ডাকসু) ‘গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক’ পদে নির্বাচিত হলে আমি গবেষণা সম্পর্কিত নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশের প্রথম রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এক বছরে অনেক কিছুই সম্ভব হবে না। কিন্তু আমি পদক্ষেপ নিয়ে ইতিবাচক ধারায় পরিবর্তন আনার কাজটা শুরুটা করতে চাই।
আমি বেশ কিছু লক্ষ্য এজন্য নির্ধারণ করেছি। এর মধ্যে আছে-
• অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তাদেরকে সেরার তালিকায় নিয়ে গেছে গবেষণার মাধ্যমে। অক্সফোর্ডের গবেষণা বরাদ্দ প্রায় ৩১ শতাংশ। আর আমাদের সেখানে মাত্র ২.০৮ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ান স্টান্ডার্ড অনুযায়ী গবেষণা বরাদ্দ মোট বাজেটের ৬ শতাংশ। আমরা আগামী এক বছরে ৬ শতাংশ না হলেও অন্তত ৪ শতাংশে নিয়ে যেতে চাই। সেক্ষেত্রে বাজেট প্রণয়নে অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করব।
• রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ ছাড়াও গবেষণা বরাদ্দ হিসেবে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উৎসের সন্ধান করতে হবে। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনকে কার্যকর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ফান্ড সংগ্রহ করতে হবে।
• ইন্ডাস্ট্রি-অ্যাকাডেমিয়া কলাবোরেশন বাড়াতে হবে। ফেলোশিপের সুবিধা আরও বাড়াতে হবে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে রিসার্চ অ্যাসিসটেন্টশিপের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য চাকরির সুযোগ তৈরি করা আমার লক্ষ্য।
• বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি ব্যবহার করে Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis, SAGE, JSTOR, Scopus, Web of Science সহ সব বড় প্রকাশনা ও ডাটাবেইসে অ্যাক্সেস আরও সহজলভ্য করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্ট্যান্ডার্ড অনলাইন লাইব্রেরী তৈরি করব।
• আমরা প্রতি বছর ‘গবেষণা মেলা’ আয়োজন করবো এবং ডাকসু নির্বাচনের তারিখের পাশাপাশি এই গবেষণা মেলাকে বিশ্বিবদ্যালয়ের বার্ষিক ক্যালেন্ডারের অন্তর্ভুক্ত করবো। আমরা মেলায় স্পনসরশিপ নিশ্চিত করব এবং দেশি ও বিদেশি বিশিষ্ট গবেষক এবং ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের আমন্ত্রণ জানাব।
• বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সামাজিক বিজ্ঞান, কলা ও চারুকলা অনুষদের সকল বিভাগ ও ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থীদের রিসার্চ মেথডলজি, রিসার্চ ডিজাইনিং, ডেটা অ্যানালাইসিস, একাডেমিক রাইটিং ও প্রপোজাল রাইটিং এর ওপর বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে অনুষদ ও হলভিত্তিক নিয়মিত মাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করব। গবেষণায় অভিজ্ঞ শিক্ষকরা এর দায়িত্বে থাকবেন। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এতে দক্ষতা লাভ করতে পারবে। বিশ্বের সকল মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সফটওয়্যার ও গবেষণায় ব্যবহৃত টুলস ফ্রিতে দিয়ে থাকে। এগুলো গবেষণাকে আরো সহজসাধ্য করে তোলে। তাই, Python, R, SPSS, NVivo, Atlas.ti, smart PLS এর মতো স্ট্যাটিসটিক্যাল টুলস ব্যবহারের কার্যকরী প্রশিক্ষণ দেওয়া।
• অনার্সের সিজিপিএর ভিত্তিতে মাস্টার্সে থিসিস নিতে পারার বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে গবেষণায় আগ্রহী শিক্ষার্থীকে থিসিস নিতে পারার সুযোগ করে দেওয়া। সকল শিক্ষার্থীকে মনোগ্রাফ ও ইন্টার্নশিপ দুটোই করার সুযোগ করে দেওয়া।
• বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত সব জার্নালের অনলাইন সংস্করণ এবং digital object identifier (DOI) থাকতে হবে। জার্নালগুলোর পিআর রিভিউয়িং প্রসেসের জন্য একটি কেন্দ্রীয় নীতিমালা রাখা।
• দেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা’ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাত্র ১৮৮টি বই প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে কিছু বইয়ের প্রাথমিক কপিও নেই। তাছাড়া শিক্ষক এবং লেখকরা ঢাবি প্রকাশনা সংস্থা থেকে বই প্রকাশের ক্ষেত্রে খুব একটা আগ্রহী নন; কারণ এটি একটি ক্লান্তিকর প্রক্রিয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা বছরে গড়ে দুই বা তিনটি বই প্রকাশ করে। এটিকে ঢেলে সাজানো আমার অন্যতম লক্ষ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসকে সচল করতে হবে। অভিজ্ঞ ও দক্ষ একজনকে এটি পরিচালনার পূর্ণকালীন দায়িত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে দেশি বিদেশি বিভিন্ন প্রেসের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে করে কাজ করা।
• ইন্ট্যারন্যাশনাল কনফারেন্সে যাওয়ার জন্য ফান্ডিং দিতে হবে। গবেষণায় অভিজ্ঞ বিদেশি গবেষক আনার ক্ষেত্রে অ্যাকোমোডেশন ও যাতায়াত খরচ বহন করতে হবে। বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে রিসার্চ কীভাবে করা হয় সেটি হাতেকলমে শেখাতে শিক্ষার্থী এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালু করব।
• বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো রিসার্চ প্রজেক্টে ৫-১০ শতাংশ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। ইন্টারডিসিপ্লিনারি রিসার্চের সুযোগ বাড়াতে হবে।
• এথিক্যাল রিভিউ বোর্ড গবেষণায় সম্পৃক্ত সকলকে নৈতিক ও আইনি সুরক্ষা দেয়। আমি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেটের কাছে একটি কেন্দ্রীয় ইন্সটিটিউশনাল এথিক্যাল রিভিউ বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করব।
• ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সেন্টারগুলোর কার্যক্রম রিভিউ ও পুনর্বিন্যাস করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৮টি গবেষণা কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউটে প্রতি বছরই বরাদ্দ আসে। এই কেন্দ্রগুলোর কয়েকটি এমনও আছে, যেগুলোতে প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনো পরিচালক নেই, অর্থাৎ এটির কোনো কার্যক্রমও নেই। তবু প্রতিবছরই এগুলোতে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। সেই টাকা অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে।আমার লক্ষ্য থাকবে যাদের রিসার্চ প্রোফাইল ভালো, তাদেরকে এসব সেন্টারগুলোর দায়িত্ব দেওয়া। শিক্ষার্থীদের জন্য রিসার্চ সেন্টারগুলোর ব্যবহার আরো সহজলভ্য করা।
• কাজের স্বীকৃতি মোটিভেশান হিসেবে কাজ করে। তাই গবেষণায় সাফল্য উদযাপন করা। অনুষদ ভিত্তিক রিসার্চ আওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা এবং অনার্স, মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি রিসার্চগুলোর অনলাইন সংস্করণ করে ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক আর্কাইভ তৈরি করা।
• বিশ্ববিদ্যালয়ের খাবার ও পানির মান পর্যবেক্ষণে নিয়মিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করা হবে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
• কন্টেন্ট ডেভলপ করে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা’কে শিক্ষার্থীবান্ধব করা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইট হালনাগাদ করে যুগোপযোগী করে তোলা সেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, অর্জন, ক্যাম্পাস লাইফ স্টাইল, ইত্যাদি ঠাঁই পাবে।’