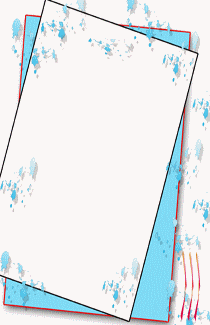সোহেল সানি :রাজনীতিতে নানা পথ অবলম্বন করেন নেতারা। তারা বেছে নেন উদারপন্থা, মধ্যপন্থা ও কট্টরপন্থা। স্বাধীনতার আগে এবং পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে উল্লিখিত তিনটি পন্থারই প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য কোন পন্থা কী পরিণতি বয়ে এনেছে, সে দিকে চোখ রাখা যেতে পারে। প্রথমেই কট্টরপন্থা নিয়ে পথচলা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের কথা বলছি। জাসদ ছাত্রলীগের একটি প্রশাখা। মুজিব বাহিনীর অন্যতম অধিনায়ক সিরাজুল আলম খানের তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ডাকসু ভিপি আ স ম আবদুর রব, ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ ও শরীফ নূরুল আম্বিয়া সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকার গঠন করে দেশে ‘বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র’ কায়েমের আহ্বান জানান। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুজিব বাহিনীর আরেক অধিনায়ক শেখ ফজলুল হক মণির নির্দেশনায় ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, ডাকসু জি এস আবদুল কুদ্দুস মাখন ও ইসমত কাদির গামা দাবি করেন, দেশ পরিচালিত হতে হবে মুজিববাদের ভিত্তিতে। তারা জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে ‘মুজিববাদ’ বলে আখ্যা দেন। ১৯৭২ সালের ১৯ জুলাই শেখ মণিপন্থি ছাত্রলীগ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং সিরাজুল আলম খানপন্থি ছাত্রলীগ পল্টন ময়দানে সম্মেলন ডাকে। উভয় গ্রুপই বঙ্গবন্ধুকে প্রধান অতিথি করে। বঙ্গবন্ধু উপস্থিত হন শেখ মণিপন্থি ছাত্রলীগের সম্মেলনে। ফলে সিরাজুল আলম খান গ্রুপ ভিন্ন পথে তাদের রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ। ছাত্রলীগের উচ্চাকাক্সক্ষী, মেধাবী, প্রতিভাবান, কট্টরপন্থি ও বিপ্লবী বলে পরিচিত অংশটি জাসদে শামিল হয়। কাজী আরেফ আহমেদ, শরীফ নূরুল আম্বিয়া, আ ফ ম মাহবুবুল হক, হাসানুল হক ইনু, খলীকুজ্জমান, নূরুল আলম জিকু, এ বি এম গোলাম মোস্তফা, শাজাহান খান, মাহমুদুর রহমান মান্না, আখতারুজ্জামান, এ বি এম শাজাহান, জিয়াউদ্দিন বাবলুসহ উদীয়মান নেতারাও জাসদের অগ্রযাত্রায় যুক্ত হন। রোমান্টিসিজম আদর্শিক ভাবালুলতা, মাঠ গরম করা ও বিপ্লবী বক্তৃতা-বিবৃতি রাতারাতি জাসদকে জনপ্রিয়তা এনে দেয়। কিন্তু অচিরেই নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও হঠকারিতায় বিপর্যয়ের সম্মুখীনও হয় দলটি।
১৯৭২ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাসদ প্রথম কাউন্সিল করে। মেজর এম এ জলিল সভাপতি, আ স ম আবদুর রব সাধারণ সম্পাদক ও শাজাহান সিরাজ যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জাসদ ঘোষণাপত্রে বলে, ‘প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েম সম্ভব নয়। শ্রেণিসংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্রকে আইনের মাধ্যমে কার্যকর করতে গেলে শোষক সম্প্রদায়কে উৎখাত করা যায় না। শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণির জঙ্গি ঐক্য গড়ে তোলার জন্য কঠোর ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজন। নির্বাচন সাধারণ মানুষকে ঠকানোর বুদ্ধি ছাড়া কিছু নয়। ভোট দেওয়ার যে রীতি তা হলো, মানুষের বিক্ষুব্ধ মনকে দমিয়ে দেওয়ার একটা কৌশল মাত্র। নির্বাচনে মেহনতি মানুষের সার্বিক মুক্তি কোনো দিন আসে না।’ আশ্চর্যের বিষয় ঘোষণাপত্রের এসব নীতিনৈতিকতা জলাঞ্জলি দিল ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চের প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই। তারা অংশ নিল। আ স ম আবদুর রব ও এম এ আউয়াল ঢাকার সংসদীয় আসনে জাতির পিতার বিরুদ্ধেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন। তারা জামানতও হারালেন। জিঘাংসা এতটাই ভয়ংকর যে, ছাত্রলীগের এই দুই সাধারণ সম্পাদক এম এ আউয়াল, আ স ম রব রাতারাতি জাতির পিতার সুদীর্ঘকালের অপরিসীম স্নেহ-ভালোবাসার কথা অবলীলায় ভুলে যেতে পেরেছেন।
জাসদ সরকারের মোকাবিলায় সশস্ত্র গোপন পন্থা অবলম্বন করে প্রকারান্তরে আত্মাহুতির পথ বেছে নিয়েছিল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে জাসদ ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্মদিনের প্রতিও সম্মান দেখানোর কথা ভুলে যায়। তারা এ জন্য ওই দিনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম মনসুর আলীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে সশস্ত্র হামলা চালায়। পুলিশের সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষের জের ধরে জাসদ কার্যত আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যায়। নেতাদের নিক্ষিপ্ত হতে হয় কারাগারে। জাসদের সশস্ত্র গণবাহিনীর প্রকাশও ছিল একটা চরমপন্থা। দলের কর্মীরা আত্মঘাতী ও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। তারা একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। জাসদ ও গণবাহিনীর সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সরকারকে উৎখাতের প্রকাশ্য ঘোষণায় যুক্ত হয় সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টি, নিষিদ্ধ ঘোষিত মাওবাদী বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিও। দেশের থানা, ফাঁড়িতে হামলা করে অস্ত্র লুট আর রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে জাসদের সংঘর্ষের খবর, আওয়ামী লীগের পাঁচজন সংসদ সদস্য হত্যা প্রভৃতি ঘটনাই বঙ্গবন্ধুকে দ্বিতীয় বিপ্লবের ‘বাকশাল’ কর্মসূচি দিতে বাধ্য করেছিল। জাসদের আরেকটি হীনমন্যতা দেশের মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। প্রথম বিজয় দিবসে রাজধানীতে নাশকতার হুংকার দেয় সর্বহারা পার্টি। অন্তরালে জাসদ। টহলরত পুলিশের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির কারণে পুলিশের গুলিতে আহত হন বঙ্গবন্ধুর পুত্র শেখ কামাল। জাসদের মুখপত্র দৈনিক গণকণ্ঠের শিরোনাম করা হলো, ‘ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে শেখ কামাল পুলিশের গুলিতে আহত’। সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা এ খবরটি প্রচার করে জাসদ চরম এক অসভ্যতার নজির স্থাপন করেছিল। জাসদের বঙ্গবন্ধুকে অস্ত্রবলে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করার দিবাস্বপ্নটিকে মনে হয় ছোট্টবেলার ‘ডাকাত-পুলিশ’ খেলা। বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হয়েছিল জাসদের কারণেই। এ দলটির কারণেই দেশ-বিদেশের ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের সম্মুখীন হন। এক কথায় জাসদই বঙ্গবন্ধু হত্যার পথ প্রশস্ত করে দেয়। ইতিহাস একদিন সাক্ষ্য দেবে, জাসদের ভ্রান্ত রাজনীতির মোহে পড়ে স্বাধীনতা-উত্তর সম্ভাবনাময় দুটি প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে গেছে।
দলটির উদ্ভট ও ভ্রান্ত রাজনীতির কারণে স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নস্যাৎ হয়েছে। ৭ নভেম্বরের তথাকথিত সিপাহি বিপ্লব ছিল জাতির জন্য এক অভিশাপ বার্তা। জাসদের গণবাহিনী ও কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা জেনারেল জিয়াউর রহমানের উত্থান ঘটায়। কিন্তু জিয়াকে দিয়ে ক্ষমতা দখলের অভিসন্ধিও নস্যাৎ হয়ে যায়। জাসদ ক্ষমতা দখলের জন্য জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীরউত্তমসহ তার সঙ্গীদের হত্যা করে। জেনারেল জিয়ার চরম বিশ্বাসঘাতকতায় কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়।
জাসদ সভাপতি মেজর এম এ জলিলের হয় যাবজ্জীবন। সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রবের ১০ বছর, হাসানুল হক ইনুর সাত বছর, মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ আরও অনেক জাসদ নেতাকে দন্ডিত হতে হয় বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ডে। পরবর্তীতে জাসদের এসব নেতা জিয়ার অনুকম্পায় মুক্তি পেলেও নিজেদের বিবাদ-বিগ্রহে দলীয়ভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যান। হায়! জাসদ ভেঙে জাসদ (আউয়াল), জাসদ (রব), জাসদ (সিরাজ), জাসদ (ইনু), জাসদ (আম্বিয়া), বাসদ (মাহবুব), বাসদ (খলিকুজ্জামান) আরও কত কী। মাহমুদুর রহমান মান্নারা তো জাসদ নামই পরিহার করে ভিন্ন পথে চলছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, জাসদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও গণবাহিনীরও অস্তিত্ব নেই। জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্রলীগেরও বিকাশ নেই। সাইনবোর্ড-সর্বস্ব একখানা ছাত্র সংগঠন মাত্র। জাসদের বহু নেতা এখন বিএনপি-আওয়ামী লীগে। জাতীয় পার্টিতেও আছেন-যারা মন্ত্রিত্বের টোপ গিলে এরশাদের চামচা বনে যান। জাসদ সভাপতি এম এ জলিল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র চুলোয় দিয়ে শেষ জীবনে ইসলামিক মুক্তি দল করেছিলেন।
শাজাহান সিরাজ ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জাসদ থেকে জয়ী হয়ে বিএনপিতে দলবলসহ বিলীন হয়ে নৌ-প্রতিমন্ত্রী হন। অবশ্য ২০০১ সালে ধানের শীষ নিয়ে জয়ী হওয়ার পর পূর্ণমন্ত্রী হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে বিএনপিতে ছিলেন অগাছা। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ১৯৯৬-২০০১ সালের মন্ত্রিসভার সদস্য হন আ স ম আবদুর রব। তখন তিনি বঙ্গবন্ধুর বন্দনা করতেন। কিন্তু ভোল পাল্টে এখন শেখ হাসিনা-বিরোধী। বঙ্গবন্ধুর কথা উচ্চারণই করেন না। আ স ম আবদুর রব ১৯৮৮ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে এরশাদের গৃহপালিত বিরোধীদলীয় নেতা বলে পরিচিত হন। জাসদের কার্যকর নেতা বলতে এখন হাসানুল হক ইনুকে বোঝায়। তাঁর নেতৃত্বাধীন জাসদ আওয়ামী লীগের ১৪ দলে রয়েছে। তিনি তথ্যমন্ত্রী ছিলেন। নিজ দলের প্রতীকে ঝুঁকি নেননি। নৌকা প্রতীকেই বারবার বিজয়ী হন। হাসানুল হক ইনুর দলেও উপদলীয় বিবাদ বিগ্রহ রয়েছে। রব, সিরাজ, ইনুরা যাদের অনুকম্পায় মন্ত্রিত্ব করেন তাদের সঙ্গে তাদের আদর্শগত বৈপরীত্য কোথায় গেল? জাসদের কঙ্কালসারশূন্য দেহবল্লরীতে নেই যৌবন। পড়ে আছে যেন দেহাবশেষ।
এবার আলোচনা করব রাজনীতির আরেকটি পথ নিয়ে। সেটি হলো- সার্বভৌম কর্তৃত্ব করা। সার্বভৌম নেতা একাই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নস্থদের ওপর চাপিয়ে দেন। নিম্নস্থদের মতামত জানতে চান না। এ কারণে যে, অবচেতন মনে নেতা আশঙ্কা করেন, নিম্নস্থ ন্যায্য কথা বলছেন, যা তার পক্ষে মানা সম্ভব নয়। এমনকি সম্মানহানিকর। নেতার এসব একাধিপত্য বেশি দিন টেকে না। অল্প সময় দলের কর্মীরা কপট আনুগত্য দেখায়, তবে অচিরেই দলে বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রতিভাবান কর্মীরা কর্মকান্ড থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়, আর যারা লোভী তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। ফলে দলে কোন্দল ও দ্বন্দ্বের মুখে স্থবিরতা নেমে আসে। এতে সার্বভৌম নেতার কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। যার ফল ভোগ করে কর্মীরা।
এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রের মতো পূর্ববাংলায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়। ১৯৫৪-এর নির্বাচন মানে হক-শহীদ-ভাসানীর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন বোঝাত। অথচ বিস্ময়কর যে, ওই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রার্থী হননি। যুক্তফ্রন্টের রূপরেখায় তিন নেতার সিদ্ধান্ত ছিল-নির্বাচনে মুসলিম লীগকে হারিয়ে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হলে পূর্ববাংলার আইন পরিষদের নেতা হবেন শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এবং পাকিস্তান গণপরিষদ নেতা হবেন সোহরাওয়ার্দী। মওলানা ভাসানীর উদার পন্থা গ্রহণ ছিল একটি দৃষ্টান্ত। ১৪৩টি আসন পেয়েও আওয়ামী লীগ শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হককে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মেনে নেয়। অবশ্য এ নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতাও আছে। মার্কিনিদের সঙ্গে সিয়াটো চুক্তিতে আওয়ামী লীগ পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ক্ষেপে যান। তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ আবার কী, আমিই আওয়ামী লীগ- আমিই মেনিফেস্টো।’ আওয়ামী লীগে তাঁর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া এতটাই তীব্র ছিল যে, সোহরাওয়ার্দীর অতি অনুগত কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানী পদত্যাগ করেন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানও নেতার বক্তব্য সমর্থন করেননি, বরং তিনি মর্মাহত হন। কট্টরপন্থি সোহরাওয়ার্দী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট শুধু ভাঙেনি, আওয়ামী লীগও কাগমারী সম্মেলনের মাধ্যমে ভেঙে যায়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। একটা পর্যায়ে পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের বলি হয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হারাতে হয়। নেতা-কর্মীদের জীবনে নেমে আসে চরম নিপীড়ন নির্যাতন। তার আগে নেতৃত্বের দ্বিতীয় প্রণালিটির কথা উল্লেখ করছি। এটি হলো, হিমশীতল, যন্ত্রবৎ, নিয়মানুবর্তী কর্মিপন্থা। অথচ হিমশীতল নিস্পৃহ পদ্ধতিতে কর্মনিপুণতা আনার চেষ্টা যথাযথ নয়। যেসব ‘মেশিন’ শাসক বা নেতার অধীনে কাজ করে তারা নিজেদের সম্পূর্ণ কর্মদক্ষতা প্রয়োগ করে না। এই পথ অবলম্বনকারীরা আক্ষরিক অর্থে পুস্তিকার আলোকে পথ চলেন। প্রতিটি প্রণালি সাধারণ বিষয়গুলোর জন্য পথনির্দেশ মাত্র-এটা তারা বুঝতে চান না। বিশ্লেষকদের মতে, এ নেতারা সাধারণ মানুষকে যন্ত্র মনে করেন। আর মানুষ যেসব জিনিস ঘোর অপছন্দ করে তার মধ্যে একটা হলো যন্ত্রের মতো আচরণ। আর তৃতীয় পন্থা অবলম্বনকারী হলেন, ‘মানবিক বোধসম্পন্ন নেতা’-যিনি শ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে পারেন। নেতৃস্থানীয় বলতে বোঝায় প্রচন্ড ব্যস্ত নেতা। নেতৃস্থানীয়রা কর্মযুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়ান। তবে নেতৃস্থানীয়রা কিন্তু বেশ খানিকটা সময় কাটান, যখন তাদের একমাত্র সঙ্গী হয় ভাবনাচিন্তা। বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষরা, প্রত্যেকেই বেশ খানিকটা সময় একা থাকতেন। অনেক নেতার মধ্যেই এভাবে উদারতার সৃষ্টি হয়, হয়ে ওঠেন মধ্যপন্থি। মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিশু, বুদ্ধ, কনফিউসিয়াস জীবনের ঘোরপ্যাঁচ থেকে দূরে একা নিজের সঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। তাঁরা একাকীত্বে পেয়েছেন চিন্তার স্বাধীনতা, চিন্তার গভীরতা।
ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট পোলিও আক্রান্ত হওয়ার পর সেরে ওঠার সময় যদি একা না থাকতেন, তাহলে আদৌ নিজের অসাধারণ নেতৃত্বের ক্ষমতা বিকশিত করতে পারতেন কি না সন্দেহ।
হ্যারি ট্রুম্যান দীর্ঘ সময় মিসোরিতে একাকী কাটিয়েছেন। অ্যাডলফ হিটলার বেশ কিছু বছর জেলজীবন কাটিয়ে ছিলেন বলেই ক্ষমতার পাহাড় গড়ে তুলেছিলেন। এই জেলে বসেই কুখ্যাত ‘মাই কেম্ফ’ লেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, যাতে বিশ্বজয়ের কূটকৌশলের উল্লেখ ছিল এবং জার্মানরা যার অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কট্টরপন্থা তাঁকে ধ্বংস করে। কমিউনিজমের কূটনীতিতে সুদক্ষ লেনিন, স্ট্যালিন, মার্কস সব নেতা জেলে বসেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্বিঘ্নে তৈরি করার সুযোগ পান। মহাত্মা গান্ধী একাকীত্বের কারণেই তাঁর ভিতরে অহিংসবাদী চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠে। একইভাবে নেলসন ম্যান্ডেলাও বিকশিত হন জেলবন্দি হয়ে। যেমন দীর্ঘ কারাজীবনে বঙ্গবন্ধুও বিকশিত হয়েছেন।
মানবিক পন্থা অনুসরণ করে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন ও তাঁর সুফলও উপভোগ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। মানবিকতাবোধের পরিণাম প্রশংসনীয় ছিল। বঙ্গবন্ধুকে গোপনেও নিন্দা করা হতো না। তিনি নিজের অধীনস্থদের কাজে বেশি নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। যে কারণে তাঁর শারীরিক অনুপস্থিতিতে সহকর্মীরা একটি সফল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দেশে ফিরে কর্মযজ্ঞেও সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পেয়েছিলেন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির চিরবন্ধুর পথ পরিহার করে যখনই সার্বভৌম ক্ষমতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্রত হলেন, তখনই নিজ দলের মধ্যেই সহকর্মীরা অনেকে ষড়যন্ত্রে যুক্ত হলো। সেই ষড়যন্ত্রের কুৎসিত চেহারা ফুটে ওঠে খুনি মোশতাকের মন্ত্রিসভায়। বঙ্গবন্ধু হত্যা গোটা বাঙালি জাতির জন্য মহা ট্র্যাজেডি। মোশতাকের পতনের পর আওয়ামী লীগের পুনর্জীবনের মাধ্যমে ‘বাকশাল’-কে না বলার মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছিল, যে ‘সার্বভৌম কর্তৃত্ব’ পন্থা অবলম্বন সঠিক ছিল না। খুনি মোশতাকও ১৫ দিনের মাথায় বাকশাল আদেশ বাতিল করে সার্বভৌম ক্ষমতার পথ এড়িয়ে চলছিলেন।
হিমশীতল যন্ত্রবৎ নিয়মানুবর্তী কর্মিপন্থা অনুসরণকারী মানে কমিউনিস্ট পন্থা। এটার প্রতিও মানুষের আস্থা সৃষ্টি হয়নি।
সংসদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সংসদীয় পদ্ধতির মধ্যে নিহিত। সংসদ সার্বভৌম অর্থ প্রকারান্তরে জনগণই সার্বভৌম। সেই সংসদের প্রধান নেতা নিঃসন্দেহে সর্বদিক দিয়ে প্রশংসনীয়। কিন্তু সদস্যরা কতটা মানবিকতাবোধ সম্পন্ন এবং এর সংখ্যা কত সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি এ দেশের মানুষের আস্থা শতভাগ। আর সেই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া খুবই কঠিন। তবে হাঁটি হাঁটি করে গণতন্ত্রের জন্যই হাঁটছে বাংলাদেশ। অবিরাম এ হাঁটার কারণেই এবং জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার বদৌলতেই শেকড় থেকে শিখরে-অগ্রসরমান সমুজ্জ্বল বাংলাদেশ।
লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক । সূএ:বাংলাদেশ প্রতিদিন